একহাতে আগুন অন্য হাতে গোলাপ
দেবাশিস চন্দ
অন্যের বিত্ত কেড়ে নেবার ইচ্ছেও নেই আমার,
কিন্তু, মনে রাখুন, খিদে পেলে
আমার ওপর চেপে বসে আছে যে, আমি
তার মাংসই তো খাব’
এর পাশে পাঠক পড়ুন চারণকবির এই দৃঢ় উচ্চারণ—
'ঘরে নেই ভাত হাঁড়ি উপোস
কাদের দোষ
জবাব চাই
জবাব না পেলে লেখনী বন্ধ করবো নাই।
ছেঁড়া কাপড়, ভাঙা অদড়—
ঘরটুকু
দুধ নেই কাঁদে খোকা খুকু
কাঁদছে ছা
কাঁদছে মা
দুখ অশেষ
এটা কি সত্যি স্বাধীন দেশ!
অন্ন নেই, বস্ত্র নেই
নেই ফুল–মধু–গন্ধ–প্রেম
‘জান দিয়ে জানোয়ার পেলেন’
ঠিক কি তাই–ই
ওষুধ নাই
রোগী মরে অনাদরে
কেনই বা
ছেঁড়া থান গায়ে কাঁদছে মা
কেন অভাব
চাই জবাব!'
জনতার মুখরিত সখ্যের সমান্তরালে কবিতার গভীরতর রহস্যময়, বিপন্ন, অনিশ্চিত গিরিখাদ— দুই বিপরীত ভুবনকে মেলানো খুব কঠিন। খুব কম কবিই তা পারেন বা পেরেছেন। চারণকবি বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (৩ সেপ্টেম্বর ১৯৩২–১৩ ফেব্রুয়ারি ২০০০) সেই বিরল গোত্রের একজন কবি যিনি জলের মতো অনায়াসে দুই ভুবন মেলাতে পেরেছেন। যেমন পেরেছিলেন নজরুল ইসলাম, সুভাষ মুখোপাধ্যায়,
বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়রা। প্রতিবাদের পাশে প্রেম অনায়াসে মিশে গেছে চারণকবির সৃজনে। প্রতিবাদী কবিতার একটা চলনে মানুষের জীবনের দুর্বিপাক, অসহায়তা, সমাজের অসাম্যের নানা ছবি তুলে ধরাই যথেষ্ট নয় মনে করে কবি সে সবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে গর্জে ওঠেন, রুখে দাঁড়ানোর ডাক দিয়ে কবিতা শেষ করেন। আর এই ফাঁক দিয়েই চোরাস্রোতের মতো কবিতার শরীরে বিষআঠার মতো লেগে যায় শ্লোগানের কাঁটাঝোপ। ফলে কবিতা আর কবিতা থাকে না। শ্লোগানে মুখরিত হয়। আর কবিতার মননশীল পাঠকমাত্রেই জানেন শ্লোগান কখনওই কবিতা নয়। নজরুল ইসলাম, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়দের কবিতায় এখানেই ব্যতিক্রমী কারণ তাঁরা জানতেন মায়াকভস্কি, পাবলো নেরুদার মতো প্রতিবাদের ফুলকিতে গোলাপের গন্ধ না আনতে পারলে সৃজন ব্যর্থ। হ্যাঁ, মায়াকভস্কি, নেরুদার লেনিন বা স্তালিন–বন্দনা করা কবিতার মতোই নজরুল, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, চারণকবি বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিছু কবিতা একবগ্গা দোষে দুষ্ট সেটা স্বীকার করেও বলতে হবে শেষ পর্যন্ত কিন্তু তাঁরা কবিতার আলো–আধাঁরির মায়াতান, রহস্যের স্বর্ণশিখরে পোঁছে গেছেন। সেজন্যই তাঁরা পাঠকের কাছে আজও আলোচনার কেন্দ্রে। পাঠকের জানা আছে, মারিও ভার্গাস লোসা নেরুদার স্তালিন–উচ্ছ্বাসে লেখা কবিতার সমালোচনা করেছিলেন, যদিও তিনি শেষ পর্যন্ত নেরুদার প্রতি তাঁর অনুরাগ মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেছেন। পাবলো নেরুদার ‘কবিত্ব’ নিয়ে তাঁর কোনও দ্বিধা ছিল না। আবার সরাসরি লিখলেই কবিতা হয় না সেটাও এক ভ্রান্ত ধারণা। সময়ের ভাষা জোগাতে, পরিবেশ, পরিস্থিতিতে কখনওসখনও কবিরা সরাসরি কথা বলে ওঠেন, অবশ্যই কবিতার ভাষাতে। সময়ের ডাক উপেক্ষা তো করতে পারেন না কোনও সমাজ সচেতন
সৃ্জনশীল লেখক। যেমন প্যালেস্টাইনের কবি মাহমুদ দারবিশের কলমে উঠে এল রাখঢাকহীন—
‘মানুষকে ঘৃণা করি না আমি,অন্যের বিত্ত কেড়ে নেবার ইচ্ছেও নেই আমার,
কিন্তু, মনে রাখুন, খিদে পেলে
আমার ওপর চেপে বসে আছে যে, আমি
তার মাংসই তো খাব’
এর পাশে পাঠক পড়ুন চারণকবির এই দৃঢ় উচ্চারণ—
'ঘরে নেই ভাত হাঁড়ি উপোস
কাদের দোষ
জবাব চাই
জবাব না পেলে লেখনী বন্ধ করবো নাই।
ছেঁড়া কাপড়, ভাঙা অদড়—
ঘরটুকু
দুধ নেই কাঁদে খোকা খুকু
কাঁদছে ছা
কাঁদছে মা
দুখ অশেষ
এটা কি সত্যি স্বাধীন দেশ!
অন্ন নেই, বস্ত্র নেই
নেই ফুল–মধু–গন্ধ–প্রেম
‘জান দিয়ে জানোয়ার পেলেন’
ঠিক কি তাই–ই
ওষুধ নাই
রোগী মরে অনাদরে
কেনই বা
ছেঁড়া থান গায়ে কাঁদছে মা
কেন অভাব
চাই জবাব!'
চারণকবির দীর্ঘ কবিতা ‘জবাব চাই’–এর (পৃষ্ঠা–১৭৮) শুরুর কয়েকটি লাইন মাহমুদ দারবিশের মতোই সোজা চোখের ওপর চোখ রেখে কথা বলে। সদ্য স্বাধীন দেশের শাসকের অন্যায়ের বিরুদ্ধে সরাসরি আঙুল তোলে কবিতার ভাষায়। একজন কবির ভাষা তো কবিতাই হয়। যে সময়ে তিনি যাপন করছেন জীবন, লিখছেন কবিতা সেই সময়ের ছবি তাঁর কবিতায় আসা অনিবার্য। সময়ের সঙ্গে, পরিবেশ, পরিস্থিতির সঙ্গে পাল্টায় সব। পাল্টায় কবির ভাষাও। কবি উইলফ্রেড এডোয়ার্ড সল্টার ওয়েন (১৮৯৩–১৯১৮) প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশ নিয়ে মারা যান। বক্সটনে থাকার সময় দশ বছর থেকে কবিতা লিখলেও তাঁকে অমরত্ব দিয়েছে চোখের সামনে দেখা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতায় লেখা ‘ভার্সেস অ্যাবাউট দ্য হররস অফ ট্রেঞ্চ অ্যান্ড গ্যাস ওয়ারফেয়ার’ কবিতাগুলি। তাঁর নিজের ভাষায়—‘মাই পোয়েমস রিফলেক্টেড এ টু জেড সোর্ড দ্যাট শো এ ক্যারেক্টার আই ডু নট ওয়ান্ট টু বি অ্যান্ড শোজ মি ফর হু আই ওয়াজ অ্যান্ড ফর হু আই ক্যান বিকাম এগেইন’। আজ ইতিহাসের দীর্ঘ পথ পেরিয়ে এসে আমরা তো ঐতিহাসিকদের পাশাপাশি ওয়নের মতো কবিদের মরমী সংবেদনশীল চোখে দেখতে চাই প্রথম এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নানা দিক, রকমারি ক্ষত। রাষ্ট্রের ভাষ্য যে সব সময়ই এক চোখা। কেবলমাত্র পেশাদার ঐতিহাসিকরা ইতিহাস লিখবেন তাঁদের নিজস্ব পড়াশোনা, দৃষ্টি দিয়ে— এই ধারণা তামাদি হয়ে গেছে। এখন ইতিহাসের নানা চোখ।
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে দেখা নানা অভিজ্ঞতার বর্ণনা, কবিতা, গদ্য, লোকগান, লোকছবি— কেউই ব্রাত্য নয় ইতিহাসের দুয়ারে। ওরাল হিস্ট্রি— মুখে মুখে বলে যাওয়া স্মৃতিনির্ভর কথারাও এখন ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ দলিল।
অর্থাৎ সময়কে ছুঁয়ে সময়াতীতের দিকে এগিয়ে যাওয়া। চারণকবি বৈদ্যনাথ সময়কে ছুঁয়ে সময়াতীতে পৌঁছে গেছেন। তিনি কালাতীত। ওয়েনের মতো চারণকবিও সময়ের দাবিতে এগিয়ে গেছেন গণআন্দোলনে সক্রিয়ভাবে। সদ্য স্বাধীন দেশের প্রত্যন্ত জেলা বাঁকুড়ার দৈন্য, দুর্দশার সঙ্গে দেশের সার্বিক পরিস্থিতি, স্বপ্ন, স্বপ্নভঙ্গ, হতাশার ছবি চিরায়ত প্রেক্ষিতে তুলে এনেছেন তাঁর কবিতায়, উপন্যাসে, নাটকে, প্রবন্ধে। আধুনিককালের একজন প্রকৃত চারণকবি বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। একদিকে নগরজীবনে মিশে যাচ্ছেন— মহানগর কলকাতা তাঁর কাছে আপন— আবার রাঢ় বাংলার মাটির স্পন্দন, বারমাস্যা তাঁর সৃজনে, চলনে জলচল। একদিকে প্রতিবাদ, আরেকদিকে প্রেম। এদিক থেকে চারণকবি বৈদ্যনাথের সঙ্গে মিল রয়েছে মৈথেলি কবি নাগার্জু বা নাগবাবার। দুজনেই জীবন রসিক, প্রেমিক কবি, আজন্ম কমিউনিস্ট। দুজনের সৃজন থেকে এটা প্রমাণিত রাজনৈতিক কবিতা এবং প্রেমের কবিতার মধ্যে নেই অহিনকূল সম্পর্ক। বাস্তবের রুক্ষ মাটিতে দাঁড়িয়ে জীবনেরই জয়গান গেয়েছেন দুই কবি, যাতে বিদ্রোহ আছে, বিরক্তি আছে, হতাশাও আছে কিন্তু দুজনেই শেষ পর্যন্ত আস্থা রেখেছেন মানুষের প্রেম, ভালবাসায়। প্রেমে, প্রতিবাদে সব্যসাচী। চারণকবি তো বলেছেনই, ‘কবিতাকে কোনও মতবাদের শৃঙ্খলে বেঁধে রাখা উচিত নয়। কবিতা তার আপন খেয়ালে, আপন উদ্দীপনায়, আপন ভাবছন্দে ছুটে চলে।’ আরেক নাগরিক কবিয়াল অ্যালেন্স গিন্সবার্গের কথাও কল্লোলিত হয়। আধুনিক সভ্যতার বিবিধ বিকৃতি, চালাকি, প্রবঞ্চনা, যুদ্ধের পাশাপাশি মানুষে বিশ্বাস না হারানোর যে কথা গিন্সবার্গের কবিতায় উঠে এসেছে এবং কবিতায় সুর দিয়ে নেচে নেচে গেয়েছেন সে সবের সঙ্গে চারণকবির মিল রয়েছে। যদিও গিন্সবার্গের মতো চারণকবি মনে করতেন না কবিতা আদতে স্বীকারোক্তি। চারণকবি মনে করেন, ‘কবিতা জবানবন্দি’, তিনি মনে করেন, ‘জিহ্বায় উচ্চারিত প্রতিটি মুক্তশব্দ কবিতা’। আরেকটু মাটির কাছাকাছি গিয়ে— যা নগর ও গ্রামের দুই পিঠ দেখা কবির পক্ষেই ভবা সম্ভব— বললেন, ‘কবিতা মানে বাঘমুণ্ডি পাহাড়ের নিচে মাদলের দ্রিমি দ্রিমি ছন্দ’।
কবিতা চারণকবির কাছে ‘জগজ্জননী—মহারাণী’। কবিতাকে জীবনের কোন গভীর সুরে বাঁধতে পারলে, অস্থিমজ্জার সঙ্গে মিশিয়ে নিতে পারলে একজন কবি বলতে পারেন কবিতা তাঁর কাছে ‘জগজ্জননী—মহারাণী’। একজন মানুষের কাছে মা–র চেয়ে বড়ো তো কেউ নন। আসলে কবিতা বৈদ্যনাথের আলো–অন্ধকার, সুখ–দুঃখ, বঞ্চনা, অনাদর, ভালবাসা, প্রেমের সঙ্গী। ১৯৪৬ থেকে ১৯৯৯—তাঁর কবিতা সৃজনের দিকে তাকালে দেখা যাবে কত রকমের কবিতাই না লিখেছেন। নানান বাঁক তাঁর কবিতায়। সেই সময়ের বাংলার, বিশেষ করে রাঢ় বাংলার কান্না–হাসি, আবেগ, মানুষের নানা দিক, সংস্কৃতির সমান্তরালে গণআন্দোলন তাঁর লেখায় তরাঙ্গায়িত হয়েছে কখনও রুদ্রবেশে, কখনও ফুলের মতো প্রেমের পরশে।
স্বাধীনতার পর সময় যত গড়াল তত চারণকবিদের সাম্যবাদের স্বপ্ন খেল বিরাট ধাক্কা। ভোগবাদ, গাড়ি, বাড়ি, বিলাস হয়ে উঠল যাপনের অঙ্গ। বৈষম্যের চোরাবালিতে ধনী–গরীরের মধ্যে ফাটল আরও বাড়ল। চারণকবিরা ক্রমশ হয়ে পড়লেন নিঃসঙ্গ, কোণঠাসা। এই বাজার–সর্বস্ব জীবন, আগ্রাসন, ভোগবাদী পরিবর্তনের দিকে তাকিয়ে তাঁর আক্ষেপ, স্বপ্নভঙ্গ,
বিপর্যয়ের কলরোল খুব স্বাভাবিক—‘জালিয়াতি রাজনীতির কয়েকটা মস্তান শুধু দেশাত্মবোধক গান গায়
কার দেশ?
কয়েকটা ধনী রক্ত পিশাচের
তাদের শাগরেদ কিছু লুটেপুটে উদর ভরায়
এদেশ তাদের ভাই লুটের মুলুক।
নিরন্ন মানুষগুলো ফ্যাকাসে দৃষ্টিতে আজ সবকিছু দেখে
দারিদ্র্যের অন্ধকারে মুখ গুঁজে অদৃষ্টেরে ধিক্কার জানায়
(এবং পশ্চিমবাংলা, পৃষ্ঠা– ২৬৬)
এবং বলতে হয় তাঁর কবিতায় আঞ্চলিক শব্দের সমৃণ ব্যবহার সেই সঙ্গে আঞ্চলিক বুলির মিশ্রণ। এত সুন্দর ছন্দেশব্দে দোলায়িত হয় যে কোথাও কোনও কৃত্রিমতার ছোঁয়া নেই। কোথাও ঠোক্কর খেতে হয় না।
নগরায়ণের নামে মেকি উন্নতি, ভোগবাদ এবং রাজনীতিবিদদের রকমারি প্রবঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে কবিতাই তাঁর আযূধ। সেই সঙ্গে তিনি নারীর মধ্যে আবিষ্কার করেছেন চিরন্ত ভালবাসার স্বরূপ যার ওপর ভিত্তি করে শত ছিন্ন, রিফু করা স্বাধীনতা–উত্তর সমাজ ব্যবস্থা টিকে আছে। ফলে হাজারো অসহিষ্ণুতার মধ্যে কবি এগিয়ে চলেন। কারণ জীবন তো থেমে থাকে না।
তিনি লিখলেন—
'এখন নতুন নাকি মূল্যবোধ তৈরি হচ্ছে ঘরে ঘেরে দেখি
একা সুখ, একা থাকা, একা বাঁচা
বড়ো জোর ছোট্ট সংসার
বেপরোয়া জীবনযাপন।
অতএব কার হাতে তুলে দেবো
পিতা প্রপিতার সেই তালপাতার পুঁথি
কে করবে মা দেখভাল
টেরাকোটা মন্দির'
(সময়–সমাজ এবং মা, পৃষ্ঠা–২৭১)
এত হতাশার মধ্যেও আশার আলো জ্বলে তাঁর অন্তরে অন্দরে। কবিতাটির শেষে তাঁর
আকুল আর্তি—
'ঘটন ও অঘটন পটিয়সী মা
আদরিণী–আহ্লাদিনী মা
পলকে পাল্টাতে পারো
এই নোংরা সমাজের রূপ'
(সময়–সমাজ এবং মা, পৃষ্ঠা–২৭১)
সাহিত্যতাত্ত্বিক ক্ষুদিরাম দাশের প্রতিধ্বনি করি বলা যায়, ‘একদিকে যেমন স্বপ্ন ও বাস্তবে মেশানো বিশিষ্ট এক পরিতৃপ্তির অনুসন্ধানী, তেমনি আধুনিক সমাজবিকৃতির বিরুদ্ধে রফাহীন বিদ্রোহ।’ তাঁর একহাতে আগুন অন্য হাতে গোলাপ। এই দুই নিয়েই তো জীবন। সৃজনজীবন। এক সাক্ষাৎকারে তাঁর অবস্থানের ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে, ‘কবি তে মহান শিল্পী, তিনি যেমন দারিদ্র্য, অভাব, শোষণের বিরুদ্ধে কবিতা লেখেন তেমনি প্রেম, ভালবাসা, নিসর্গকে নিয়েও কবিতা লিখতে পারেন।’ হ্যাঁ, তিনি বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মিলিয়েছেন দুই প্রান্তকে। তিনি চারণকবি আগুন ও গোলাপে কোনও বিরোধ দেখতে পান না। তাঁর ‘রূপশালি মেয়ে’, ‘নূপুর বোষ্টমী’, ‘পুষ্পমাসী, ‘হে বনমরালী’, ‘প্রেমপুষ্প’, ‘চিঠি’, ‘তালপাতার বাঁশি’, ‘কানামাছি’, ‘কুমারী অঞ্জনা’র মতো লিরিক কবিতায় চিরায়ত প্রেম, ভালবাসার হরেক স্তর, নানা রং। প্রতীক্ষা, কামনা, বিরহ, আর্তি। ‘কানামাছি’–তে যদি থাকে হৃদয়ের আর্তি, তাহলে ‘নূপুর বোষ্টমী’তে নেই কোনও চাওয়া, সেখানে শুধু ত্যাগের মহত্ব। ‘কুমারী অঞ্জনা’য় প্রতীক্ষার চূড়ান্ত টানাপোড়েন। কবিতাগুলোতে বৈষ্ণব পদাবলির রামধনু আলো। যেমন, ‘দোষ কী?’ কবিতাটি—
‘রাই জাগো রাই জাগো... পদাবলী কীর্তন
ধূপের গন্ধ, শুকসারী করে ঝগড়াফিস ফিস কথা হলে ফের হবে নিন্দা
দ্বারে উঁকি মারে চঞ্চলমতি বৃন্দা।
কবিতাটির শেষ লক্ষ্য করুন—
'টিপ খসে গেছে, আলগা যমুনা–গঙ্গা—
শাড়ির আঁচল, আলুথালু মেঘ কুন্তল,
তবু সারা মুখে কেন যে ছড়ানো লজ্জা
দোষ কী যদি গো ফের হয় ফুলশয্যা।।’
আত্মজীবনী ‘একটি প্রচ্ছদপটের গল্প’–তে তাঁর ভাবনা পরিস্কার করেছেন, ‘নিষ্কাম ভালবেসে নির্মল আনন্দ খুঁজে বেরিয়েছি সারা জনম।... দেহকে ঘিরে দেহের উর্দ্ধে দেহাতীত প্রেমে মুগ্ধ হতে না পারলে কী আমার দেশের এই নরম মাটিতে সৃষ্টি হতে পারতো বৈষ্ণব পদাবলী?’ তাঁর কবিতায় আধুনিকতা বা তথাকথিত উত্তর–আধুনিকতার নামে নেই কোনও রাংতা মোড়া চকমকি। আলটপকা শব্দ ব্যবহারে চমক লাগানোর ব্যর্থ চেষ্টা। তাঁর কবিতা হৃদয় উপচানো ভালবাসার আলোয় আলোকিত, আন্তরিক, নদীর জলের মতো চির বহমান। সেই জন্যই হয়তো বাংলা সাহিত্যের মূল ধারায় থেকে গেছেন অনেকটা উপেক্ষিত, কারণ আলোচকরা ধরতে পারেননি তাঁর সুর। ঈশ্বর গুপ্ত, রামপ্রসাদ, মুকুন্দ দাস, গোবিন্দ দাসদের লোকায়ত ধারার সার্থক উত্তসূরী চারণকবি। পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত নাগরিক সাহিত্য আলোচকরা এই ধারাটির প্রতি প্রবল উন্নাসিকতায় নাক সিঁটকোন বলেই চারণকবিরা থেকে যান ইতিহাসে উপেক্ষিত। বঞ্চিত হন প্রাপ্যসম্মান থেকে। তবে ইতিহাস তো ফিরে তাকায় কোনও এক সময়। বারবার সেটা প্রমাণিত। সেই ফিরে
দেখায় সসম্মানে উঠে আসেন চারণকবিরা। এভাবেই ফিরে আসবেন, এসেছেন চারণকবি বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। কবিতার জন্য তিনি বিশেষ পরিচিত হলেও চারণকবি বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্য–উপন্যাস ‘ঘেঁটু’, উপন্যাস ‘অনুরক্তা নায়িকা’, ‘রেণু নেই, বসন্ত নেই, রক্তসন্ধ্যা’, অনু–উপন্যাস ‘কর্ণ সোমের ডায়েরি’, দুটি নাটক ‘রঙের গোলাম’, ‘পথ’–এর কথা ভুললে চলবে না। ছোটদের জন্য লিখেছেন জমজমাট ছড়ার বই ‘আম–কাঁঠালের ভোজ’। তাঁর আত্মজীবনী ‘একটি প্রচ্ছদপটের গল্প’ তো অন্তরঙ্গ ফুলকি, উদ্যাপনের জলতরঙ্গ। তাঁর অনেক গদ্য এবং প্রবন্ধ রয়ে গেছে অগ্রন্থিত। কবির সম্পাদিত ‘খড়্গ’–এর সম্পাদকীয়গুলিও উদ্ধার করে দুই মলাটের মধ্যে এবার ঢেউ তুলুক। তীক্ষ্ণ, তীব্র, আক্রমণাত্মক আবার একই সঙ্গে তির্যক সম্পাদকীয়গুলি ‘শনিবারের চিঠি’র সজনীকান্ত দাসের স্মৃতি উসকে দেয়। কোদালকে কোদাল বলতে তাঁর হাত কাঁপেনি। সম্পাদকীয়গুলো সঙ্কলিত হলে আমরা খুঁজে পাব এক নতুন বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তাঁর তাঁর জ্যোষ্ঠপুত্র কবি–সাংবাদিক–সম্পাদক স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা থেকে জানা যায় ‘কেষ্টনগরের পুতুল’ এবং ‘একটি প্রচ্ছদপটের কান্না’ গল্প দুটির কথা। পুতুলগড়ার কারিগরদের পুতুলে রূপান্তরিত হয়ে যাওয়ার কাহিনী ‘কেষ্টনগরের পুতুল’, যা বেরিয়েছিল অমলজ্যোতি দাস সম্পাদিত ‘খরাভূমি’ পত্রিকায়। আর ‘একটি প্রচ্ছদপটের কান্না’ প্রকাশিত হয় চারণকবির নিজের কাগজ ‘শিল্পী’–তে। পার্কে রাত কাটানো এক দুঃখী, বোহেমিয়েন কবির পকেট মারতে এসে ধরা পড়ে একজন মহিলা পকেটমার। এ সংসারের তীব্র অভাব থেকে পকেটমারের কাজে নামা মহিলার জীবনকথা কী অসাধারণ দক্ষতা ও বাঁধুনীতে তুলে এনেছেন চারণকবি ভাবা যায় না। এই গল্পের নাম অনুসরণে চারণকবি পরবর্তীতে তাঁর আত্মকথার নাম রাখলেন ‘একটি প্রচ্ছদপটের গল্প’। স্বপন লিখছেন, ‘কারণ বোধহয়, কবির গল্পের এই অভাবী নায়িকাটির মতো তাঁর জীবনও যন্ত্রণাময় চলচ্চিত্র। সে কারণেই হয়তো এই নামকরণ। তাঁর সৃষ্ট নায়িকার কান্না মুছে নিজের জীবনের গল্প হয়ে গেছে।’ হিজড়েদের নিয়ে এই সময়ে বাংলা সাহিত্যে কিছু লেখালেখি হচ্ছে। বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গত শতকের পাঁচের দশকে সাহস দেখিয়েছিলেন সমাজ পরিত্যক্ত, ব্যঙ্গ–বিদ্রুপের শিকার হিজড়েদের প্রান্তিক ভুষোকালির মতো অন্ধকার জীবনে প্রবেশের তাঁর উপন্যাস ‘রেণু নেই, বসন্ত নেই’ উপন্যাসের মাধ্যমে। সাহিত্যিক স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় ‘মাসিক বসুমতী’ প্রকাশের জন্য নিয়ে গিয়ে পাণ্ডুলিপিটি হারিয়ে ফেলেন। দুর্ভাগ্য লেখক বৈদ্যনাথের। তবু মন্দের ভাল উপন্যাসটির একটি সংক্ষিপ্ত রূপ গল্প হিসেবে ছাপা হয় মেজিয়ার ‘দীপ্তি’ পত্রিকায়। মিনি সাইজের বইয়েরও তিনিই প্রথম প্রবর্তক। গত শতকের পাঁচের দশকের মাঝামাঝি সময়ে অসুস্থ স্ত্রীর চিকিৎসার টাকা জোগাড়ের জন্য লেখেন অনু–উপন্যাস ‘কর্ণ সোমের ডায়েরি’। বইটি প্রকাশ করেছিলেন মিনি বইয়ের আকারে। ‘স্ট্রিম অফ কনশাসনেস’– ‘চেতনা প্রবাহ রীতি’র অণু–পরমাণুর অন্ত নাই যে অনন্ত অনুভূতি তিরতির করে বয়ে চলেছে উপন্যাসের শরীরে। জাহাজের ডেকে বসা নীরব, চিন্তিত কর্ণ সোমের হাতে একের পর এক সিগারেট ধোঁয়া হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। সেই ধোঁয়ায় ভেসে উঠছে অদ্ভুত সব নারী অবয়ব। যেন শিল্পীর তুলিতে আঁকা। তারা সিগারেটের ধোঁয়ার মতো কর্ণের ভাবনায়, চেতনায় ধরা দিচ্ছে, থাকছে, আবার হারিয়ে যাচ্ছে। চিন্তা–ভাবনা, আঙ্গিকে অত্যন্ত আধুনিক এই উপন্যাস তুলনীয় জেমস জয়েসের ‘ইউলিসিস’–এর সঙ্গে।
লিখেছেন বেশ কিছু নতুন ভাবনার প্রবন্ধ। বিশেষ করে বলতে হয় রাঢ় বাংলার তন্ত্রের প্রভাব নিয়ে প্রবন্ধটির কথা। নাটক রচনাতেও রেখেছেন উজ্জ্বল সাক্ষর। তাঁর ‘রঙের গোলাম’ এবং ‘পথ’ ছাপার আলো দেখেনি। ফলে আজ আর পড়ে দেখার উপায় নেই। জানাচ্ছেন তিনি, ‘গণনাট্যর হয়ে কাকাবাবুর নির্দেশে (মুজফ্ফর আহমেদ) উত্তরবঙ্গ যেতে হয়েছিল নাটক নিয়ে। তখনই লেখা ‘রঙের গোলাম’। পরে সেই নাটক কলকাতায় ও বাঁকুড়া–বিষ্ণুপুরের গ্রামেগঞ্জেও অভিনীত হয়েছে অসংখ্যবার। ‘রঙের গোলাম’ই প্রথম যাত্রাধর্মী একাঙ্ক নাটক, যেখানে রূপকের আড়ালে শোষণের কথা বলা হয়েছে। আর আমার লেখা ‘পথ’ ছিল প্রথম স্ট্রিট ড্রামা। তারপরেই কলকাতা–সহ সারা দেশে এ ধরণের নাটকের সূচনা।’ অভিনয় করেছেন যাত্রা ও চলচ্চিত্রে। এক বহুমুখী প্রতিভা। এক যথার্থ বর্ণময় ব্যক্তিত্ব। আজ তাঁর নব্বইতম জন্মদিনে দাঁড়িয়ে ভাবতে ভাল লাগছে এই মানবপ্রেমিক, আকাশের মতো মুক্ত, উদার, সমুদ্রের মতো বিশাল হৃদয়ের লোকটির সঙ্গে চলার পথে পরিচয় হয়েছিল। দেখা যে খুব বেশি হয়েছিল তা নয়। কিন্তু যখনই দেখা হয়েছে তাঁর ভালবাসার বৃত্তে টেনে নিয়েছেন যেখানে ছিল মৃগনাভির গন্ধের মতো অমোঘ আকর্ষণ, ফুলের পাপড়ি মেলার মতো কত না বিস্ময়ের উন্মোচন। তাঁর আন্তরিক আত্মকথা ‘একটি প্রচ্ছদপটের গল্প’–তেও সামান্য এই শব্দশ্রমিককে
জায়গা দিয়েছেন। যা এক বিরাট পাওয়া তো বটেই। তাঁর গলায় স্বরচিত কবিতা পাঠ শোনা যেন তৃষ্ণার শান্তি। সে তাঁর বাড়িতে বসে হোক বা কোথাও কোনও আসরে আলখাল্লা পরিহিত অবস্থায় নেচে নেচে কবিতা পাঠই হোক— যাঁরা শুনেছেন তাঁরা জানেন ভাল কবিতা পাঠ কাকে বলে। স্মৃতি থেকে একের পর এক কবিতা ঝরনার কলস্বরের মতো ঝরে পড়ে ভিজিয়ে দেয় মেধার শুকনো প্রকোষ্ঠ। ঈর্ষণীয় ছিল তাঁর কণ্ঠস্বর। তাঁর পাঠ–জাদুতে ভেসে যেত শিক্ষিত নাগরিক থেকে গ্রামের আনপড় লোকজন। মনে পড়ছে, বাঁকুড়ার বেলিয়াতোড়ে কবি মোহন সিংহরা একবার চারণকবিকে সম্বর্ধনা দিয়েছিলেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে কলকাতা থেকে গিয়েছিলেন অমিতাভ দাশগুপ্ত এবং পবিত্র মুখোপাধ্যায়। সঙ্গে কলকাতার কয়েকজন কবি। সেই দলে কীভাবে যেন জুটে গিয়েছিল জায়গা। ছিল লেখক আফসার আহমেদও। আমরা সবাই হইহই করে সকালের ট্রেন ধরে হাওড়া থেকে পৌঁছে গেলাম যথাসময়ে। অনুষ্ঠান শেষে অনেক রাত পর্যন্ত আড্ডা, চারণকবির নাচের সঙ্গে কবিতা পাঠ। চমক অপেক্ষা করছিল পরের দিন সকালে। আমাকে আর আফসারকে বললেন, চল্ বিষ্ণুপুরে আমার বাড়ি। আজ বিকেলে শুরু হচ্ছে বিষ্ণুপুর মেলা। মেলা দেখবি। আমার বাড়িতে থাকবি। প্রসঙ্গত, সেই বছরই প্রথম চালু হয় বিষ্ণুপুর মেলা। আমি তো এক পায়ে খাড়া। আগে কখনও যাইনি মন্দির–শহরটিতে। আফসারও রাজি হল। সঙ্গে পরিচয়ের সঙ্গে যুক্ত আমাদের বন্ধু পার্থপ্রতিম কুণ্ডু। বাসে রওয়ানা দিলাম বিষ্ণুপুর চারজনে। পৌঁছে পাঁঠার মাংস ও অন্যান্য আনুসাঙ্গিক জিনিসপত্র কিনলেন আমাদের অতিথি সেবা করবেন বলে। আগের দিন সম্বর্ধনা সভায় কিছু অর্থ উপহার
পেয়েছেন। অতএব চির–বাউণ্ডুলে কবিকে আর কে পায়! তিনি এখন রাজা! বাড়ি পৌঁছে স্নান, খাওয়াদাওয়া শেষে দিবানিদ্রা। সন্ধেবেলা মেলার উদ্বোধনে অনুষ্ঠান। সবই হল। আসল চমক অপেক্ষা করছিল এরপর। মেলা থেকে ফিরে এসে দেখি একদল বাউল হাজির। অতিথিদের গান শোনানোর ব্যবস্থা করেছেন বাড়ির কবি–মালিক। একটু রাত হতেই শুরু হল ঠাকুর ঘরে কালী–আরাধনা। যা চলল অনেক রাত পর্যন্ত।কপালে লাল তিলক, রক্তাভ পোষাকে সজ্জিত কবির তখন আরেক রূপ। উদাত্ত কণ্ঠে মন্ত্রপাঠ আর মা মা ডাকে এক আধিভৌতিক পরিবেশ। মরার খুলিতে কারণবারি পান। সব কিছু দেখে আফসার তো ভয়ে কাঠ। রীতিমতো কাঁপছে। এখনও এত এত বছর পরেও আফসারের ভীতসন্ত্রস্ত মুখ চোখে ভাসে। সে এক অভিজ্ঞতা বটে। কোনওদিন ভুলব না। চারণকবির এই কালীভক্তি, পুজোআচ্চা নিয়ে অনেকেই নাক সিঁটকেছেন, হাওয়ায় হাওয়ায় ভেসেছে তেরচা সব কথা— মার্কসবাদে বিশ্বাসী একজন কমিউনিস্ট কী করে এভাবে পাল্টে যান! এই বিচ্যূতি মেনে নেওয়া যায় না। আমার কিন্তু মনে হয়েছে কালীর মধ্যে দিয়ে তিনি ‘মা’ তথা ‘মেয়ে’–কে খুঁজেছেন, দেখেছেন। বৃহত্তর অর্থে দেশ ও দশের ‘মা’ তথা ‘মেয়ে’। নানা কারণে পার্টি–রাজনীতির প্রতি একটা সময়ের পর তাঁর বিতৃষ্ণা আসে, দূরত্ব তৈরি হয়। এই দূরত্ব মানসিক, ভাবগত। পার্টি–রাজনীতির প্রতি যে রকম দূরত্ব তৈরি হয়েছিল শিল্পী সোমনাথ হোরের। নানা বিচ্যূতি দেখে নিজের লেখালেখিতে সোমনাথ হোর স্বীকার করেছেন, দল থেকে দূরে এসে ভালই করেছেন। যদিও মার্কসবাদে তাঁর বিশ্বাস অটূট ছিল জীবনের শেষ মাইলস্টোন পর্যন্ত। চারণকবি বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়েরও মার্কসবাদে বিশ্বাস টলে যায়নি। আর্তের কান্নায় সাড়া দিয়েছেন, মানুষের ডাকে ছুটে গেছেন আজীবন। জীবনের একটা সময়ের পরে সেই পথে ছিল না কোনও দলীয় ঝাণ্ডা। আর মার্কসবাদে বিশ্বাস মানে তো কোনও বিশেষ পার্টির রাজনীতিতে অন্ধের মতো সায় দেওয়া নয়। যেমন জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস মানে তো একটি বিশেষ দলের সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদী, সাম্প্রদায়িক মনোভাবে বিশ্বাস রাখা নয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে ন্যাশনালিজম–জাতীয়তাবাদের কথা বলেছেন সেই জাতীয়তবাদ কোনও সঙ্কীর্ণ গণ্ডিতে, ডোবায় আটকে নেই। তাতে বিশ্বাস করা যায়। আস্থা রাখা যায় না ওই বিশেষ দলের সঙ্কীর্ণ জাতীয়তবাদে। চারণকবি সক্রিয় রাজনীতি থেকে দূরে সরে এলেও মার্কসবাদ বা কল্যাণকামী জাতীয়তাবাদ থেকে তো দূরে সরে যাননি। শক্তিসাধাক তথা শাক্ত এই কবির কালী উপসনায় অন্ধ ভক্তিভাব ছিল না। ছিল না কোনও সঙ্কীর্ণ গোঁড়ামী। ছিল শেষ বয়সে শান্তির তীর খোঁজা। রামপ্রসাদের মতো তিনিও কালীকে সামনে রেখে খুঁজেছেন জীবনের মানে, তার সমস্যা, বেদনা, আনন্দ, দুঃখ, নিপীড়ণ। কালীচেতনার মধ্যে দিয়ে রামপ্রসাদের মতোই চারণকবিও ব্রহ্মাণ্ডের বিশাল বিস্তৃতি, মহান চেতনাকে ছোঁয়ার চেষ্টা করেছেন, মানব কল্যাণের স্বরূপ বুঝতে চেষ্টা করেছেন। রামপ্রসাদের মতো সংশয়ে দীর্ণ হয়েছেন। ‘ব্রহ্মাণ্ড ছিল না যখন মুণ্ডুমালা কোথায় পেলি?’— রামপ্রসাদের মতো চারণকবিও বলছেন—
‘আমার বুকের রক্তজবা—যায় শুকিয়ে, ঝরুক মিছে
যেমন আছি থাকবো আমি রাখ না ফেলে সবার নিচে।’
(দস্যি মেয়ে, পৃষ্ঠা–১৩০)
আবার কখনও তাঁর আকুল জিজ্ঞাসা—
‘তুমি কি মৃন্ময়ী শুধু?
তুমি নও সাধকের জন্মদাত্রী মা!
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রসবিনী
পুত্রবতী—স্বদেশ–জননী!
এভাবেই আজীবন চিনেছি তোমাকে
মৃন্ময়ী চিন্ময়ী সত্ত্বা’
তারপর পরিস্কার করছেন তাঁর কাছে ‘পূজা’র অর্থ—
‘পূজা মানে ভালোবাসা প্রেম
মন্ত্র মানে সত্যশব্দ কম্বুকণ্ঠে উচ্চারিত ধ্বনি।’
(সময়–সমাজ এবং মা, পৃষ্ঠা–২৬৮)
রবীন্রনাথ ঠাকুরের ‘আরাধনা’র মতো, ‘দেবতাকে প্রিয় করি, প্রিয়কে দেবতা’র মতো চারণকবিও কালী–আরাধনার মধ্যে দিয়ে খুঁজেছেন নিজেকে, খুঁজেছেন মহাকালকে, খুঁজেছেন মানুষকে। প্রকৃত সাধককবির মতো তিনি কালীর মধ্যে মানুষকে পেয়েছেন, মানুষের মধ্যে কালীকে। তাঁর কালী–চেতনা, কালী আরাধনা তো প্রকারান্তরে ব্রহ্মাণ্ড চেতনা। যা ধর্মের ক্ষুদ্র গণ্ডি পেরিয়ে এক মহত্তর মানব প্রেমে উত্তীর্ণ, যা মানুষের সর্বাঙ্গীন কল্যাণে ঝঙ্কৃত। ধর্মের ছোট্ট, ঝাপসা ঠুলি চোখে লাগিয়ে তাকালে যাঁর মহত্ব বোঝা অসম্ভব।
তাঁর চেতনার রঙে আলোকিত হয় মানবভূমি, মানুষই তাঁর কাছে শেষ কথা। মানবপ্রেম তাঁর আরাধ্য।বৈষয়িক জীবনে উদাসীন, যথার্থই বোহেমিয়ান এই কবি নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন জনহিতার্থে। কখনও নিজের কথা ভাবেননি। ভেবেছেন সমষ্টির কথা। তাঁর জ্যোষ্ঠপুত্র স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিতে সংসারে সন্ন্যাসী মানুষটির অমলিন ছবি, ‘অন্যের বাবারা যেভাবে সংসারকে আলো দেন, লণ্ঠনে তেল আছে কিনা খোঁজ করেন, তিনি এসব সাংসারিক ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে ভাবেননি। পরিবর্তে ভেবেছেন অটল তাঁতির কথা। ভেবেছেন ভুলকা টুডুর কথা। ফলে সংসার ছেড়ে তিনি বেরিয়ে পড়েছেন ওইসব সমষ্টিগত শোষিত মানুষের মুক্তির সন্ধানে।... অসহায়–নিরন্ন অসংখ্য মানুষের ঘরে আলো জ্বালাতে হবে। তারই সন্ধানে ঘুরে
বেড়াচ্ছেন কবি। ঘুরে বেড়াচ্ছেন একজন রাজনৈতিক কর্মী। হ্যাঁ, জ্বালাময়ী কবিতা নিয়েই তিনি তখন তিনি কমিউনিস্ট আদর্শে বিশ্বাসী একজন মানুষ। আর এই শোষিত–বঞ্চিত অসংখ্য মানুষের মধ্যে থাকতে থাকতেই তিনি নিজেকে ভুলেছেন। ভুলেছেন নিজের সংসারকে।... সমষ্টিগত ভাবনাই আন্দোলিত হয়েছে জীবনভর।’
(আমার বাবা: চারণকবি বৈদ্যনাথ, পৃষ্ঠা– ৮৬, প্রামাণ্য চারণকবি বৈদ্যনাথ, সম্পাদনা কাজল চক্রবর্তী, প্রকাশক সাংস্কৃতিক খবর, ২০১৯)।
মাইকেল মধুসূদন দত্ত, নজরুল ইসলামের মতোই সাংসারিক জীবনের তথাকথিত সুখ মুঠোবন্দি করতে পারেননি। পারেননি কারোর মন জুগিয়ে চলতে। ফলে বাংলা সাহিত্যের কোনও পুরস্কার তাঁর ঝুলিতে ঢোকেনি। রবীন্দ্রসদনে রাজ্য সরকার আয়োজিত কবিতা পাঠের অনুষ্ঠানে ডাক পড়েনি। এতটা অবহেলা তাঁর বোধহয় কাম্য ছিল না। যদিও তিনি এ সব নিয়ে কখনও ভাবেননি। সাজানো, বকুলবিছানো রাজপথ ছেড়ে নিজের মতো করে পথ তৈরি করে এগিয়েছেন সমাজ–সংসারের রীতিনীতির তোয়াক্কা না করে। তাঁর বক্তব্য স্পষ্ট, ‘আমি সৃষ্টির আনন্দেই মাতাল। কী হল আর কী হল না এ সব নিয়ে মাথা–ব্যাথা নেই। কারও পায়ে তেল দিইনি কখনও। নিজেকে বিকিয়ে দিইনি অসত্যের কাছে। তাই হয়তো আমার ঘরে পুরস্কারের বন্যা নেই। প্রচারের সার্চলাইট নেই। যা আছে সেটা হল পরম সত্য। সেই সত্যই একদিন আলোকিত করবে আমার ভুবন। আমার সৃষ্টিকে।’ তিনি চেয়েছেন মানুষের মধ্যে মিশে যেতে—
‘নিজেরে বিলাতে চাই নিখিলের গণ–আন্দোলনে’
এবং তিনি চান তাঁর কবি–শিল্পী সত্ত্বাটুকু থাক বেঁচে আগামীর দুয়ারে—
‘রক্তের আলপনা এঁকে এঁকে
আমি শুধু চলে যাবো
শিল্পীর পদাঙ্কটুকু রেখে।।’
(শিল্পী, পৃষ্ঠা–২৮৫)
হ্যাঁ, চারণকবি বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেঁচে আছেন, থাকবেন তাঁর সমস্ত সৃজন–ঐশ্বর্য নিয়ে।
এবং তিনি চান তাঁর কবি–শিল্পী সত্ত্বাটুকু থাক বেঁচে আগামীর দুয়ারে—
‘রক্তের আলপনা এঁকে এঁকে
আমি শুধু চলে যাবো
শিল্পীর পদাঙ্কটুকু রেখে।।’
(শিল্পী, পৃষ্ঠা–২৮৫)
হ্যাঁ, চারণকবি বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেঁচে আছেন, থাকবেন তাঁর সমস্ত সৃজন–ঐশ্বর্য নিয়ে।
লেখায় উদ্ধৃত কবিতাগুলি নেওয়া হয়েছে ‘চারণকবি বৈদ্যনাথের নির্বাচিত কবিতা’ থেকে। প্রকাশক চারণকবি বৈদ্যনাথ সাহিত্য আকাদেমি, ২০১২)







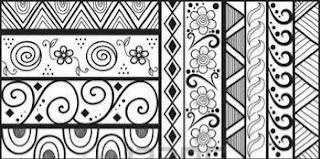

No comments:
Post a Comment